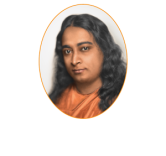বাবাজি: মহাবতার বাবাজি দ্রষ্টব্য।
বেদ: হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থ বেদ চার প্রকার: ঋক, সাম, যজুর ও অথর্ব। এরা মূলত ভজন, পূজন ও মন্ত্রোচ্চারণমূলক একটি সাহিত্য, যার উদ্দেশ্য মানবজীবনের বিভিন্ন পর্যায় ও কর্মধারাকে উজ্জীবিত ও অধ্যাত্মধর্মী করে তোলা। ভারতের বিপুলসংখ্যক ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে বেদই (সংস্কৃত বিদ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ “জ্ঞাত হওয়া”) একমাত্র গ্রন্থ, যার কোনো সুনির্দিষ্ট রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। এই মন্ত্রগুলির দৈবী উৎসের কথা উল্লেখ করে ঋগ্বেদ বলে এগুলি পুরাকাল থেকে নতুন নতুন ভাষার আচ্ছাদনে চলে আসছে। যুগ যুগ ধরে সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের কাছে দিব্যজ্ঞানরূপে প্রকাশিত এই চতুর্বেদ কালের বিচারে ‘নিত্যত্ব’ প্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়।
বেদান্ত: আক্ষরিক অর্থ “বেদের অন্ত”; যে দর্শন উপনিষদ বা বেদের শেষ ভাগ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। শঙ্করাচার্য (অষ্টম বা নবম শতাব্দীর গোড়ার দিকে) ছিলেন বেদান্তের প্রধান ব্যাখ্যাকার; বেদান্ত ঘোষণা করে যে ঈশ্বরই একমাত্র সত্য এবং সৃষ্টির যা কিছু আমরা দেখতে পাই, সে সব নিছকই মায়া বা বিভ্রান্তি। যেহেতু মানুষই একমাত্র প্রাণী যে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা করতে সক্ষম, তাই সে স্বয়ং অবশ্যই দিব্যগুণসম্পন্ন এবং নিজের আসল প্রকৃতি উপলব্ধি করাই তার কর্তব্য।
বৈশ্বিক ধ্বনি: ওম দ্রষ্টব্য।
বৈশ্বিক প্রাণশক্তি: প্রাণ দ্রষ্টব্য।
বৈশ্বিক বিভ্রম: মায়া দ্রষ্টব্য।
বোধযুক্ত বৈশ্বিক স্পন্দন: ওম দ্রষ্টব্য।
ব্রহ্মচৈতন্য (বৈশ্বিক চেতনা): পরব্রহ্ম; সৃষ্ট জগতের ঊর্ধ্বে যে পরমাত্মা। ধ্যানে সমাধি অবস্থায় ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হলে সৃষ্ট জগতের ঊর্ধ্বে ও স্পন্দমান বিশ্বের ভিতরে যে অনুভব হয়। ত্রিত্ব দ্রষ্টব্য।
ব্রহ্মন (ব্রহ্মা): পরমাত্মা। সংস্কৃতে ব্রহ্মনকে মাঝে ব্রহ্মা (শেষে হ্রস্ব আ কার চিহ্ন দিয়ে) বলে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু এর অর্থ ব্রহ্মন এর সমার্থক অর্থাৎ পরমাত্মা বা পরমপিতা, এখানে কিন্তু সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ত্রয়ীর পরিচিত ধারণাকে বোঝান হয় নি (সেখানে ব্রহ্মার শেষে দীর্ঘ আকার ব্যবহার হয়েছে)। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব দেখুন।
ব্ৰহ্মা-বিষ্ণু-শিব: সৃষ্টির মধ্যে পরিব্যাপ্ত ঈশ্বরের তিন রূপ। খ্রিস্টচৈতন্য বা কূটস্থচৈতন্য (তৎ) যা বৈশ্বিক প্রকৃতির সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই তিন ধরণের কাজকেই পরিচালনা করে, এঁরা তারই প্রতিভূ।ত্রিত্ব দ্রষ্টব্য।
ভক্তিযোগ: ঈশ্বরমিলনের একটি আধ্যাত্মিক পন্থা। এতে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগস্থাপন ও তাঁর সঙ্গে অভিন্নতাবোধের উপায় হিসেবে পূর্ণসমর্পিত প্রেমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যোগ দ্রষ্টব্য।
ভগবদ্গীতা: “ঈশ্বরের সঙ্গীত”। গীতা একটি আঠারো অধ্যায় বিশিষ্ট প্রাচীন ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ যেটি মহাভারতের ষষ্ঠ পর্বের (ভীষ্ম পর্ব) অন্তর্গত। ঐতিহাসিক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে ভগবান কৃষ্ণ ও তাঁর ভক্ত শিষ্য অর্জুনের মধ্যে কথোপকথনাকারে রচিত গীতা যোগবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি গভীর জ্ঞান-সমন্বিত গ্রন্থ, প্রাত্যহিক জীবনে সুখ ও সাফল্যের জন্য যার ব্যবহার চিরকাল ধরে নির্দেশিত আছে। গীতা একাধারে রূপক এবং ইতিহাস; মানুষের অন্তরে শুভ ও অশুভ প্রবৃত্তির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছে, সে সংক্রান্ত এক আধ্যাত্মিক ভাষ্য হল গীতা। বিষয়বস্তু অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন গুরু, আত্মা কিংবা ঈশ্বরের প্রতীকস্বরূপ। আর অর্জুন হলেন সাধনমার্গের উৎসাহী এক ভক্ত। এই বিশ্বজনীন ধর্মগ্রন্থখানির প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন, “যারা গীতার বাণী নিয়ে ধ্যান করবে, তারা প্রতিদিন তা থেকে নতুন করে আনন্দ ও অর্থ আহরণ করতে পারবে। এমন কোনো আধ্যাত্মিক গ্রন্থ নেই যা গীতা উন্মোচন করতে পারে না।”
ভগবান কৃষ্ণ: ভগবান কৃষ্ণ একজন অবতার যিনি জিশু খ্রিস্টের জন্মের বহু পূর্বে ভারতে বসবাস করতেন। হিন্দুশাস্ত্রে কৃষ্ণ নামের অন্যতম একটি অর্থ হল: “সর্বজ্ঞ পরব্রহ্ম”। সুতরাং খ্রিস্টের মতো কৃষ্ণও একটি আধ্যাত্মিক উপাধি, যা ঈশ্বরের সঙ্গে একজন অবতারের অভেদত্বরূপ আধ্যাত্মিক বিশালত্বের দ্যোতনা বহন করে। ভগবান উপাধির অর্থ হল ঈশ্বর। ভগবদ্গীতায় তাঁর যে বাণী লিপিবদ্ধ আছে, তা বলার সময় তিনি উত্তর ভারতের এক রাজ্যের নৃপতি ছিলেন। বাল্যকালে তিনি ছিলেন একজন গোপালক যিনি তাঁর বাঁশির সুরে সঙ্গীদের মোহিত করে রাখতেন। কৃষ্ণের এই গোপালকের ভূমিকাটিকে অনেক সময় রূপকার্থে আত্মার প্রতিভূ হিসেবে দেখা হয়, যিনি ধ্যানের মুরলীধ্বনি শুনিয়ে বিপথগামী চিন্তাগুলিকে পুনরায় সর্বজ্ঞতার পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।
মনুষ্য: এই শব্দটি সংস্কৃত মানস যেখান থেকে এসেছে সেই একই মূল থেকে এসেছে, মন—বাস্তব চিন্তা করার মৌলিক মানবীয় ক্ষমতা। যোগ বিজ্ঞান মানুষের চেতনাকে এমন এক দিক দিয়ে বিচার করে যা মূলত লিঙ্গবোধযুক্ত সত্ত্বার ঊর্ধ্বে (আত্মা)। যেহেতু ইংরেজি ভাষায় এই ধরণের মনস্তাত্ত্বিক এবং আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশ করার মত পরিভাষা নেই, অতিরিক্ত ভাষাগত জটিলতা সৃষ্টি না করে, মনুষ্য এবং তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য শব্দ এই প্রকাশনায় রেখে দেওয়া হয়েছে –তবে মনুষ্য শব্দের সংকীর্ণ অর্থে তা ব্যবহার করা হয়নি কারণ তাহলে মানবজাতির শুধু অর্ধ অংশকেই বোঝানো হবে এখানে মনুষ্য শব্দকে তার বৃহত্তর প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
মন্ত্রযোগ: একটি ইষ্টমন্ত্র যার মধ্যে আধ্যাত্মিকভাবে কল্যাণকর স্পন্দনময় শক্তি আছে, তাকে ভক্তিপূর্ণচিত্তে গভীর একাগ্রতার সঙ্গে জপ করার মাধ্যমে যে ঐশ্বরিক সংযোগস্থাপন সাধিত হয়, তাকে মন্ত্রযোগ বলে। যোগ দ্রষ্টব্য।
মহাবতার বাবাজি: ইনি সেই মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবতার যিনি ১৮৬১-তে লাহিড়ী মহাশয়কে ‘ক্রিয়াযোগে’(দ্র) দীক্ষিত করার মাধ্যমে মুক্তিদায়িনী ওই প্রাচীন পদ্ধতিটিকে পৃথিবীতে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিলেন। চিরযৌবনের অধিকারী এই মহাবতার বহু শতাব্দী ধরে হিমালয়ে অবস্থান করে পৃথিবীকে সর্বদাই আশীর্বাদধন্য করে চলেছেন। বাবাজীর জীবনের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর প্রেরিত মহাত্মাদের বিশেষ কার্যক্রমে সহায়তা করা। তাঁর অতীব আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থার পরিচয়বাহী বিভিন্ন নামে তাঁকে সম্বোধিত করা হলেও মহাবতার সাধারণত সাদাসিধে ‘বাবাজি’ নামটিকেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর জীবন ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য সম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য যোগী-কথামৃত গ্রন্থে পাওয়া যাবে। অবতার দ্রষ্টব্য।
মহাসমাধি: মহাযোগীর শেষ ধ্যান বা সচেতন ঈশ্বরসংযোগ, যখন তিনি ভৌত শরীর ত্যাগ করে মহাপ্রণবে বিলীন হয়ে যান। একজন সদগুরু পূর্বাহ্নেই নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন, তাঁর দেহনিকেতন ত্যাগ করার জন্য ঈশ্বর কোন সময়টি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সমাধি দ্রষ্টব্য।
মা ভগবতী: ঈশ্বরের সেই স্বরূপ যা সৃষ্টির মধ্যে ক্রিয়াশীল; পরমেশ্বরের শক্তি। এই ঐশ্বরিক রূপের আরও কয়েকটি নাম আছে, যেমন প্রকৃতি, ওম, পবিত্র আত্মা (Holy Ghost), বোধসম্পন্ন বৈশ্বিক স্পন্দন ইত্যাদি। এছাড়াও, ঈশ্বরের সেই মাতৃসত্তাবিশিষ্ট রূপ যার মধ্যে দিয়ে তাঁর অপার ভালোবাসা ও করুণা প্রকাশ পায়।
হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী ঈশ্বর যেমন সৃষ্টির সব কিছুতেই অনুস্যূত হয়ে আছেন, তেমনই তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বেও বিরাজ করছেন; একই সঙ্গে যেমন তিনি ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট, তেমনই আবার নৈর্ব্যক্তিকও। তাঁকে যেমন অদ্বৈত পরব্রহ্মরূপে, তেমনই প্রেম, জ্ঞান, আনন্দ, জ্যোতি — তাঁর এইসব চিরন্তন গুণাবলির যে কোনো একটিকে নিয়েও আমরা আরাধনা করতে পারি। অথবা তাঁকে আমরা ‘ইষ্ট’ রূপে, কিংবা পরমপিতা, জগন্মাতা, সখা রূপেও ভজন করতে পারি।
মায়া: সৃষ্টির কাঠামোর মধ্যেই নিহিত যে প্রপঞ্চময় শক্তির প্রভাবে এক বহু রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকেই ‘মায়া’ বলে। মায়া হল আপেক্ষিকতা, বৈপরীত্য, বৈসাদৃশ্য, দ্বৈতাবস্থা, পরস্পরবিরোধী অবস্থার মূল কারণ। এই মায়াকেই বাইবেলের প্রথমাংশে (Old Testament) ধর্মপ্রবর্তকগণ ‘শয়তান’ (হিব্রুভাষায় যার অর্থ “প্রতিপক্ষ”) বলে অভিহিত করেছেন; এই সেই ‘পিশাচ’ যাকে জিশু চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন খুনে ও মিথ্যাবাদীরূপে, কারণ তার ভেতর কণামাত্রও সত্য নেই (জন ৮:৪৪)।
পরমহংস যোগানন্দ লিখেছেন, “সংস্কৃত ভাষায় মায়া শব্দের অর্থ পরিমাপক; এ হল সৃষ্টির এমনই এক ঐন্দ্রজালিক শক্তি যার দ্বারা ‘অপরিমেয়’ ও ‘অবিচ্ছেদ্যকে’ আপাতদৃষ্টিতে পরিমেয় এবং বিভাজ্য বলে অনুমিত হয়। মায়া স্বয়ং এই প্রকৃতি — চতুর্দিকে পরিদৃশ্যমান এই যে জগত যা ঐশ্বরিক নিত্যতার বৈপরীত্য হিসেবে সততই পরিবর্তনের অধীন। ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও লীলা অনুযায়ী, শয়তান বা মায়ার একমাত্র কাজই হল ঈশ্বরের কাছ থেকে জড় বস্তুর দিকে, সত্য থেকে অসত্যের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য চেষ্টা করে যাওয়া।”
মাস্টার: যিনি নিজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনলাভে সক্ষম হয়েছেন। গুরুর (দ্র) উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা সহকারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পরমহংস যোগানন্দ বলেছেন, “গুরুর বৈশিষ্ট্য হল তাঁর আধ্যাত্মিকতা, কোনো জাগতিক মাপকাঠিতে তাঁর বিচার চলে না…ইচ্ছামাত্র শ্বাসহীন অবস্থায় (সবিকল্প সমাধি) প্রবেশ করা এবং নির্বিকল্প সমাধিতে অপরিবর্তনীয় আনন্দ আস্বাদন করা – কারো এই দুই সামর্থ অর্জিত হলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি গুরু হওয়ার পদবাচ্য।” সমাধি দ্রষ্টব্য।