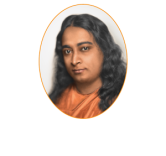গুণ: বিশ্বপ্রকৃতির ত্রিগুণাত্মিকা রূপ, সমগ্র সৃষ্টি যার বশীভূত। এই তিনটি গুণ হল যথাক্রমে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব; অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতা, ক্রিয়াশীলতা ও ব্যাপ্তি; অথবা দ্রব্য, শক্তি ও বৌদ্ধিক তত্ত্ব। মানুষের মধ্যে তিনটি গুণ প্রকাশ পায় যথাক্রমে—অজ্ঞানতা বা জড়তা, কর্মপ্রবণতা বা সংগ্রাম, এবং জ্ঞান বা প্রজ্ঞা।
গুরু: আধ্যাত্মিক শিক্ষক। যদিও গুরু শব্দটি প্রায়শই যে কোনো শিক্ষকের সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়, একজন প্রকৃত ঈশ্বরদ্রষ্টা গুরু হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি তাঁর নিজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণলাভে সক্ষম হয়েছেন এবং সর্বব্যাপী পরমাত্মার সঙ্গে তাঁর একাত্মতা অনুভব করতে পেরেছেন। একজন ঈশ্বরসন্ধানীকে তাঁর দিব্য অনুভূতিলাভের পথে আন্তর যাত্রায় পথপ্রদর্শন করার ক্ষেত্রে এরকম একজন গুরুই হলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। যখন এক ভক্ত একান্তভাবে ঈশ্বরসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তখন ভগবান তার জন্য একজন গুরুকে পাঠিয়ে দেন। সেই গুরুর জ্ঞান, বুদ্ধি, আত্মানুভূতি ও উপদেশের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর ভক্তকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন। গুরুর শিক্ষা ও অনুশাসনকে অনুসরণ করে শিষ্য ঈশ্বরপ্রাপ্তিরূপ আহারের জন্য তার আত্মিক বাসনা চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়। সত্যসন্ধানী ভক্তদের অন্তরের আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের সাহায্য করার জন্য ঈশ্বরের নির্দেশে যে গুরু এগিয়ে আসেন, তিনি কখনোই একজন সাধারণ শিক্ষক নন। তিনি হলেন মানবদেহধারী এমনই এক বাহন, যাঁর দেহ, মুখনিঃসৃত বাক্য, মন ও আত্মিকতাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে ঈশ্বর পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদের আকর্ষণ করেন যাতে তারা তাদের দিব্যধামে ফিরে যেতে পারে। শাস্ত্রোক্ত সত্যের মূর্তিমান প্রতিরূপ হলেন শ্রীগুরু। তিনি হলেন মুক্তির দূত; জড়বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য ভক্তের আকাঙ্ক্ষাপূরণের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর তাঁকে নিযুক্ত করেন। স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর তাঁর দ্য হোলি সায়েন্স (The Holy Science) বইতে লিখেছেন, “গুরুর সঙ্গলাভের জন্য শুধু তাঁর শারীরিক উপস্থিতিতে থাকাটাই সব নয় (কারণ কোনো কোনো সময় সেটা প্রায় অসম্ভব), কিন্তু প্রধানত এর অর্থ হল, তাঁকে আমাদের হৃদয়ে স্থান দেওয়া এবং নীতিগতভাবে তাঁর সাথে একাত্ম হওয়া, এবং তাঁর সাথে সমন্বয়বিধান করে চলা।”
গুরুদেব: “অধ্যাত্ম শিক্ষাগুরু” – সংস্কৃত ভাষায় শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি প্রচলিত শব্দ যা কোনো অধ্যাত্ম গুরুর উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে; কখনও কখনও ইংরেজি ভাষায় “মাস্টার” বলেও অভিহিত করা হয়।
চক্র: যোগশাস্ত্র অনুযায়ী মানবদেহের মেরুদন্ড ও মস্তিষ্কে প্রাণ ও চৈতন্যের সাতটি অতিপ্রাকৃত কেন্দ্র আছে। এরাই মানুষের জড় ও সূক্ষ্মদেহকে প্রাণবন্ত করে তোলে। এই কেন্দ্রগুলিকেই চক্র (“চাকা”) বলা হয়, কারণ এদের প্রত্যেকের মধ্যে যে ঘনীভূত শক্তি রয়েছে, তা অনেকটা চক্রনাভির মতো যেখান থেকে জীবনদায়িনী জ্যোতি ও শক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে। ঊর্ধ্বক্রমানুযায়ী এই চক্রগুলির নাম হল: ‘মূলাধার’ (মেরুদন্ডের তলদেশে); ‘স্বাধিষ্ঠান’ (মূলাধার থেকে দুই ইঞ্চি ওপরে); ‘মণিপুর’ (নাভির বিপরীতে); ‘অনাহত’ (হৃৎপিণ্ডের বিপরীতে); ‘বিশুদ্ধ’ (ঘাড়ের মূলদেশে); ‘আজ্ঞা’(ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত; প্রকৃতপক্ষে বিপরীত প্রান্তে সুষুম্নাশীর্ষকের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত; আরো দেখ সুষুম্নাশীর্ষক ও অধ্যাত্ম নেত্র ); এবং ‘সহস্রার’ (মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ স্থান বা ব্রহ্মতালুতে অবস্থিত)। ঈশ্বরীয় পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত এই সাতটি কেন্দ্রকে বাইরে যাওয়ার রাস্তা বা “মেঝের দরজা” বলা যেতে পারে যেগুলোর মধ্য দিয়ে আত্মা দেহে অবতরণ করে এবং যেগুলো অতিক্রম করে ধ্যানের সাহায্যে আত্মা আবার ঊর্ধ্বগামী হয়। পরপর সাতটি ধাপ পেরিয়ে আত্মা ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে মুক্তিলাভ করে। মস্তিষ্ক-মেরুদন্ডগত সাতটি চক্র উন্মুক্ত বা “জাগ্রত” হলে সেগুলোর মধ্য দিয়ে আত্মা সচেতনভাবে ঊর্ধ্বমুখী পথে অনন্তের দিকে উন্মুক্ত রাজপথ ধরে যাত্রা শুরু করে, কারণ সেটাই প্রকৃত পথ যার মধ্য দিয়ে আত্মাকে তাঁর উৎস ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হওয়ার পথ খুঁজে নিতে হবে। যোগশাস্ত্র গ্রন্থগুলিতে সাধারণত নীচের ছ-টি কেন্দ্রকেই চক্র বলা হয়; সহস্রারকে পৃথকভাবে সপ্তম কেন্দ্র বলা হয়ে থাকে। তবে সাতটি কেন্দ্রকে প্রায়ই পদ্ম নামে অভিহিত করা হয় যার পাপড়িগুলি মেরুদন্ডের মধ্য দিয়ে প্রাণ ও চেতনার উত্তরণের সাথে সাথে আধ্যাত্মিকভাবে জাগ্রত হয়ে উন্মীলিত হয় বা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে।
চিত্ত: স্বজ্ঞালব্ধ অনুভূতি; চেতনার সমষ্টি, যার মধ্যে সহজাত থাকে অহংকার, বুদ্ধি ও মানস (মন বা ইন্দ্রিয়জ চেতনা)।
চেতনা, বিভিন্ন পর্যায়ের: জাগতিক চেতনায় মানুষের তিনটি অভিজ্ঞতা হয়: জাগ্রত চেতনা, নিদ্রিত চেতনা ও স্বপ্নময় চেতনা। কিন্তু অতিচেতন অবস্থা বা তার আত্মার অনুভূতি সে পায় না এবং ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতাও সে লাভ করে না। কিন্তু খ্রিস্ট চেতনার মানুষ, তা লাভ করেন। শরীরধারী মানুষের চেতনা যেমন তার সারা শরীর ব্যাপী, খ্রিস্ট চেতনার মানুষের চেতনাও তেমনিই সারা বিশ্বব্যাপী, যাকে সে তার নিজের শরীর হিসেবেই অনুভব করে। খ্রিস্ট চেতনার ঊর্ধ্বে রয়েছে বৈশ্বিক চেতনা; সেই বৈশ্বিক চেতনা হল পরম চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি। স্পন্দন যুক্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে যে শুদ্ধ চৈতন্যরূপী অব্যয় পরব্রহ্ম আছেন এবং ব্যক্ত জড় জগতের সর্বত্র তাঁর যে প্রকাশ ঘটছে, তারই সঙ্গে একীভূত হওয়ার অভিজ্ঞতা।
জাতি: জাতি সম্বন্ধে মূল যে ধারণা, তাতে বংশপরম্পরার কোনো স্থান ছিল না; বরং মানুষের স্বাভাবিক কর্মদক্ষতা অনুযায়ী এই শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছিল। বিবর্তনের পথে মানুষকে সুনির্দিষ্ট চারটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা এই চারটি স্তরের নাম দিয়েছিলেন যথাক্রমে ‘শূদ্র’, ‘বৈশ্য’, ‘ক্ষত্রিয়’ ও ‘ব্রাহ্মণ’। শূদ্র শ্রেণিভুক্ত যারা, তারা সচরাচর শারীরিক প্রয়োজন ও বাসনা পরিতৃপ্তিতেই আনন্দ লাভ করে। উন্নতির যে পর্যায়ে সে পৌঁছেছে, তাতে দৈহিক শ্রম করার পক্ষেই সে সবচেয়ে উপযুক্ত। যারা বৈশ্য, তারা পার্থিব ধনসম্পদবৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টি করাতেই আগ্রহী হয়। শূদ্রের থেকে তার সৃজনশীল ক্ষমতা বেশি এবং কৃষিকর্ম, ব্যবসা, শিল্পকর্ম বা অন্য যেসব কর্মে তার মানসিক শক্তি তৃপ্তিলাভ করে, সেই সকল কর্মে সে নিযুক্ত হতে ভালোবাসে। বহু জন্মের ভেতর দিয়ে শূদ্র ও বৈশ্য হিসেবে তাদের যাবতীয় বাসনা চরিতার্থ করার পর ক্ষত্রিয় শ্রেণিভুক্ত মানুষজন এই প্রথম জীবনের অর্থ খুঁজতে শুরু করে; সে তার বদভ্যাসকে জয় করতে, ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে এবং শুভকর্ম সম্পাদন করতে সচেষ্ট হয়। ক্ষত্রিয়রা সাধারণত পেশায় মহৎ শাসক, কূটনীতিজ্ঞ এবং যোদ্ধা হয়ে থাকে। যারা নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে জয় করেছে, তারাই হল ব্রাহ্মণ; আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাদের স্বাভাবিক ঔৎসুক্য থাকে; তারা ভগবৎজ্ঞানী হয় এবং সেজন্য অন্যকে শিক্ষাদান করতে ও তার মুক্তিলাভের জন্য সাহায্য করতে সক্ষম হয়।
জ্ঞানযোগ: ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য বুদ্ধির বিচারবিশ্লেষণী ক্ষমতাকে আত্মার সর্বজ্ঞতায় রূপান্তরকরণের এক সাধনমার্গ।
তত্ত্ব: পঞ্চতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।
ত্রিত্ব: সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে পরমাত্মা নিজেকে ত্রিত্বস্বরূপে প্রকাশ করেন: সৎ, তৎ, ওম বা পিতা, পুত্র ও দিব্য আত্মা। পিতা (সৎ) হলেন স্রষ্টারূপী ঈশ্বর যিনি সৃষ্টির ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন (ঈশ্বরীয় চৈতন্য)। পুত্র (তৎ) হলেন সৃষ্টিতে বিদ্যমান ঈশ্বরের সর্বব্যাপী বুদ্ধিমত্তা (কূটস্থ চৈতন্য)। আর দিব্য আত্মা (ওম) হল ঈশ্বরের স্পন্দনশীল শক্তি যা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। অনন্তকাল ধরে বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়ের কালচক্র বার বার এসেছে এবং চলেও গেছে (যুগ দ্রষ্টব্য)। প্রলয়কালে ত্রিত্ব এবং সৃষ্টির সঙ্গে আপেক্ষিক সম্বন্ধযুক্ত সমগ্র জগৎ অসীম পরমাত্মায় মিলিয়ে যায়।
দর্শন: “পবিত্র দৃশ্য” যেমন নিজ গুরু; ঈশ্বর উপলব্ধিকারী এক সত্ত্বার দর্শন পাওয়া অর্থে তাঁর আশীর্বাদ লাভ।
দীক্ষা: অধ্যাত্মপথে প্রবেশমূলক অনুষ্ঠান। সংস্কৃত ভাষায় মূল ক্রিয়াপদ ‘দীক্ষ’ শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ নিজেকে উৎসর্গ করা। শিষ্য এবং ক্রিয়াযোগ দ্রষ্টব্য।
ধর্ম: ন্যায়পরায়ণতার চিরন্তন নীতি যা সমস্ত সৃষ্টিকে ধারণ করে আছে; এই সব নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে জীবনযাপন করাই মানুষের স্বাভাবিক কর্তব্য। সনাতন ধর্ম দ্রষ্টব্য।
ধ্যান: গভীর একাগ্রতা সহ ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হওয়া। এই শব্দটি দিয়ে সাধারণভাবে কোনো একটি প্রক্রিয়ার অনুশীলনকে বোঝায় যার দ্বারা মনোযোগকে অন্তর্মুখী করে ঈশ্বরের কোনো একটি বৈশিষ্ট্যের ওপর একাগ্র হওয়া যায়। তবে ধ্যান বলতে বিশেষ করে এই সব প্রক্রিয়ার সঠিক অভ্যাসের পর যে ফল পাওয়া যায়, তাকেই বোঝায় — এর অর্থ হল স্বজ্ঞালব্ধ অনুভূতির দ্বারা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করা। মহর্ষি পতঞ্জলি বর্ণিত অষ্টাঙ্গ যোগের এটা সপ্তম ধাপ (ধ্যান); এই অবস্থাপ্রাপ্তি তখনই সম্ভব, যখন কেউ নিজের অন্তর্দেশে এমন সুগভীর একাগ্রতা অর্জন করতে সক্ষম হয় যাতে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা তাকে আর আদৌ বিক্ষুব্ধ করতে পারে না। ধ্যানের চূড়ান্ত অবস্থায় সাধক যোগের অষ্টম ধাপ বা সমাধির অভিজ্ঞতা অর্জন করে, যার অর্থ ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগস্থাপন বা তাঁর সঙ্গে একাত্মতা। পতঞ্জলি দ্রষ্টব্য।